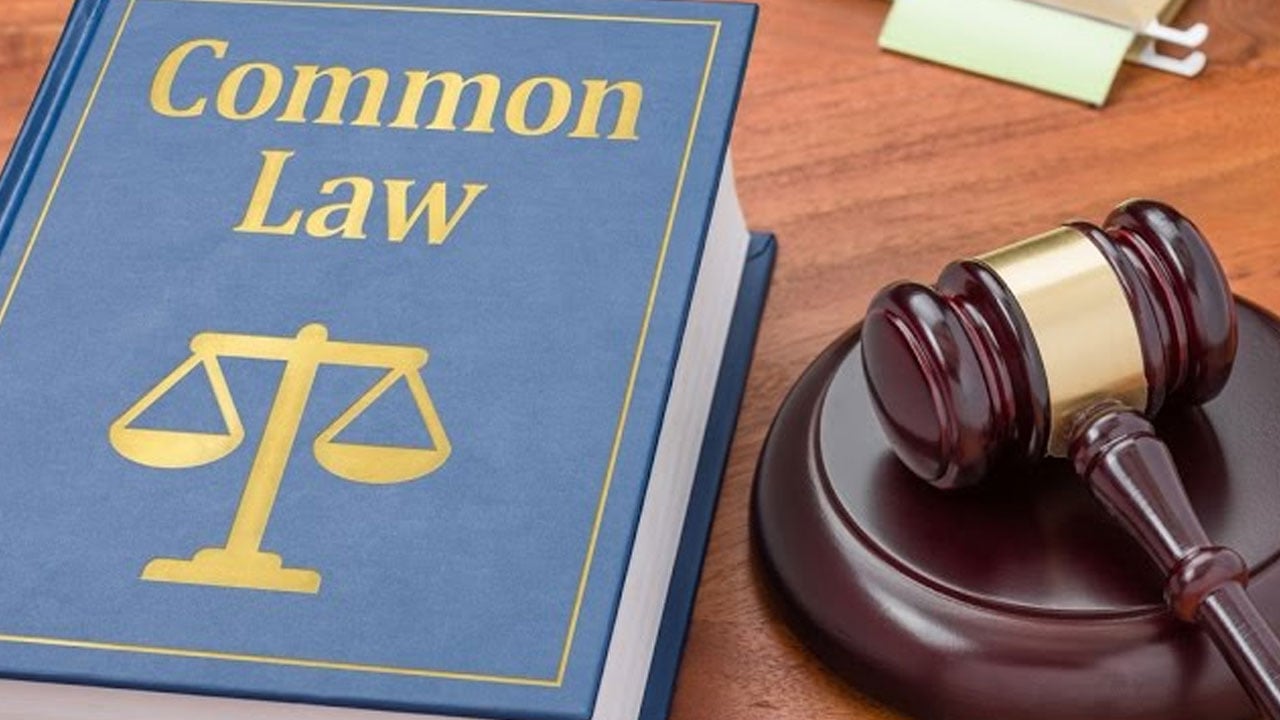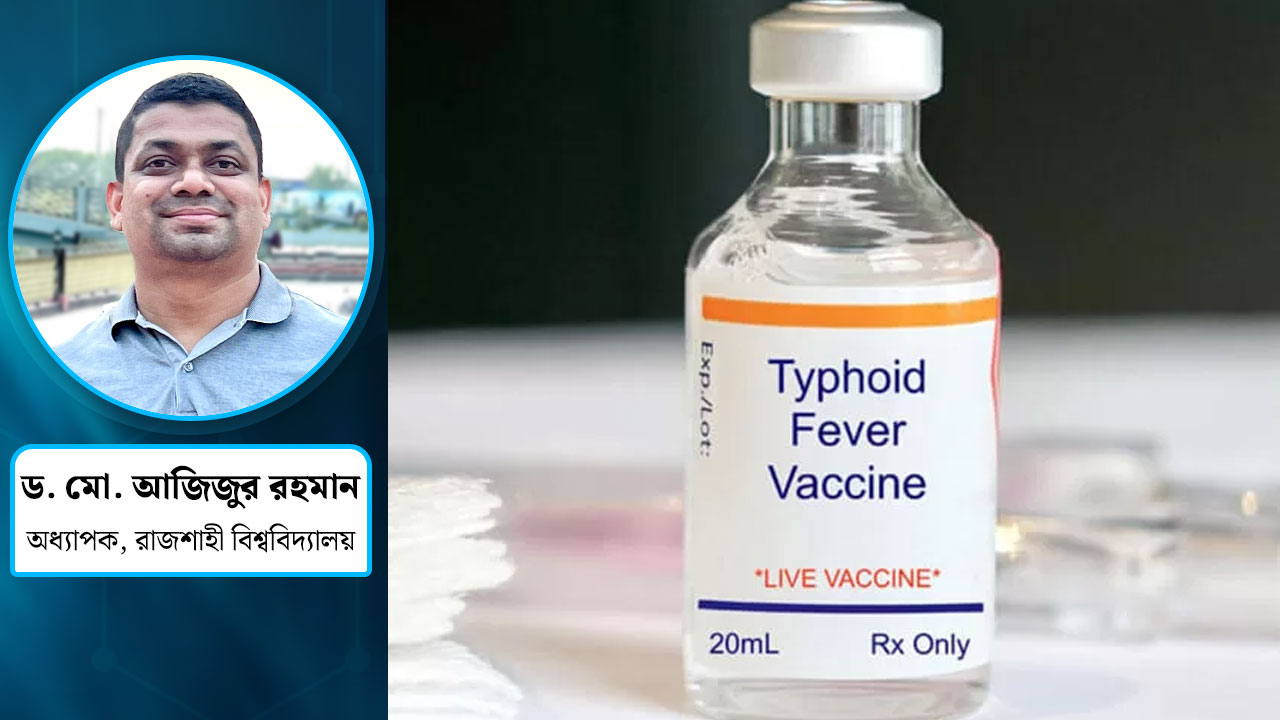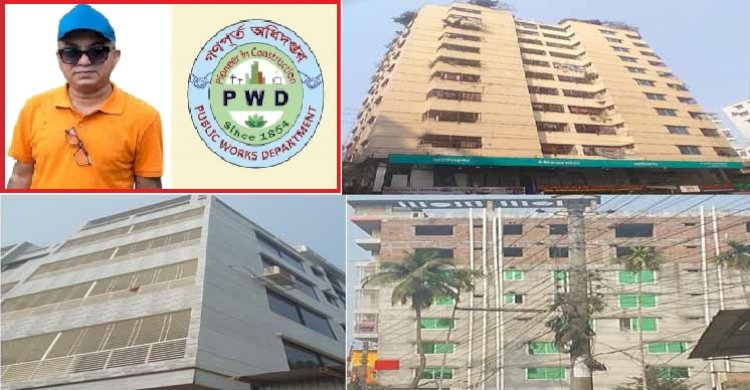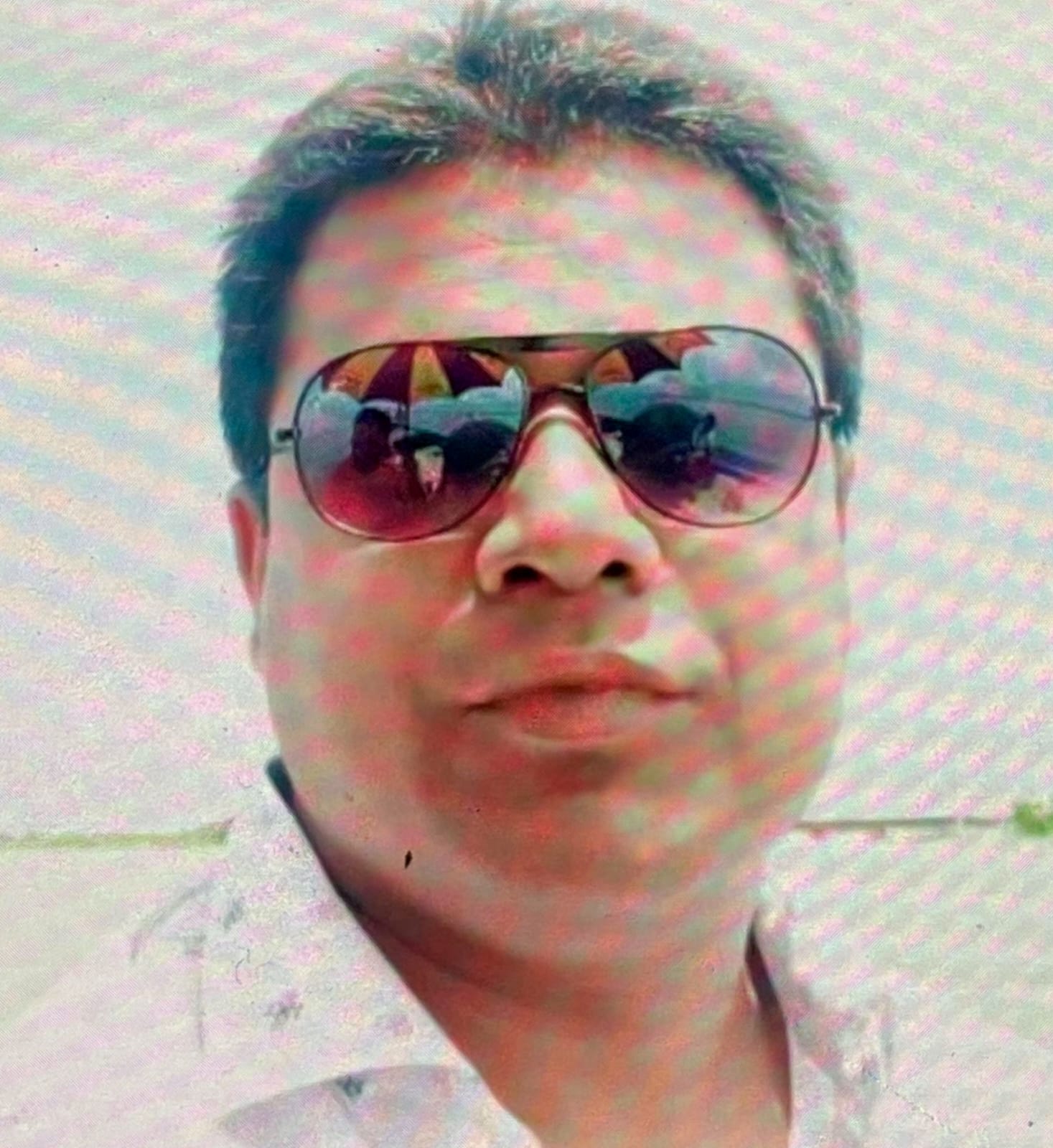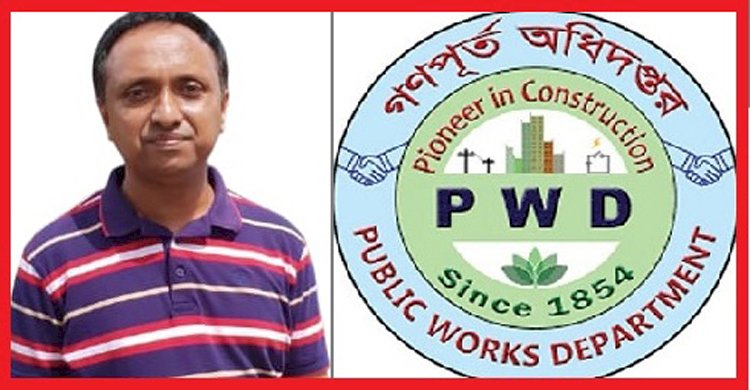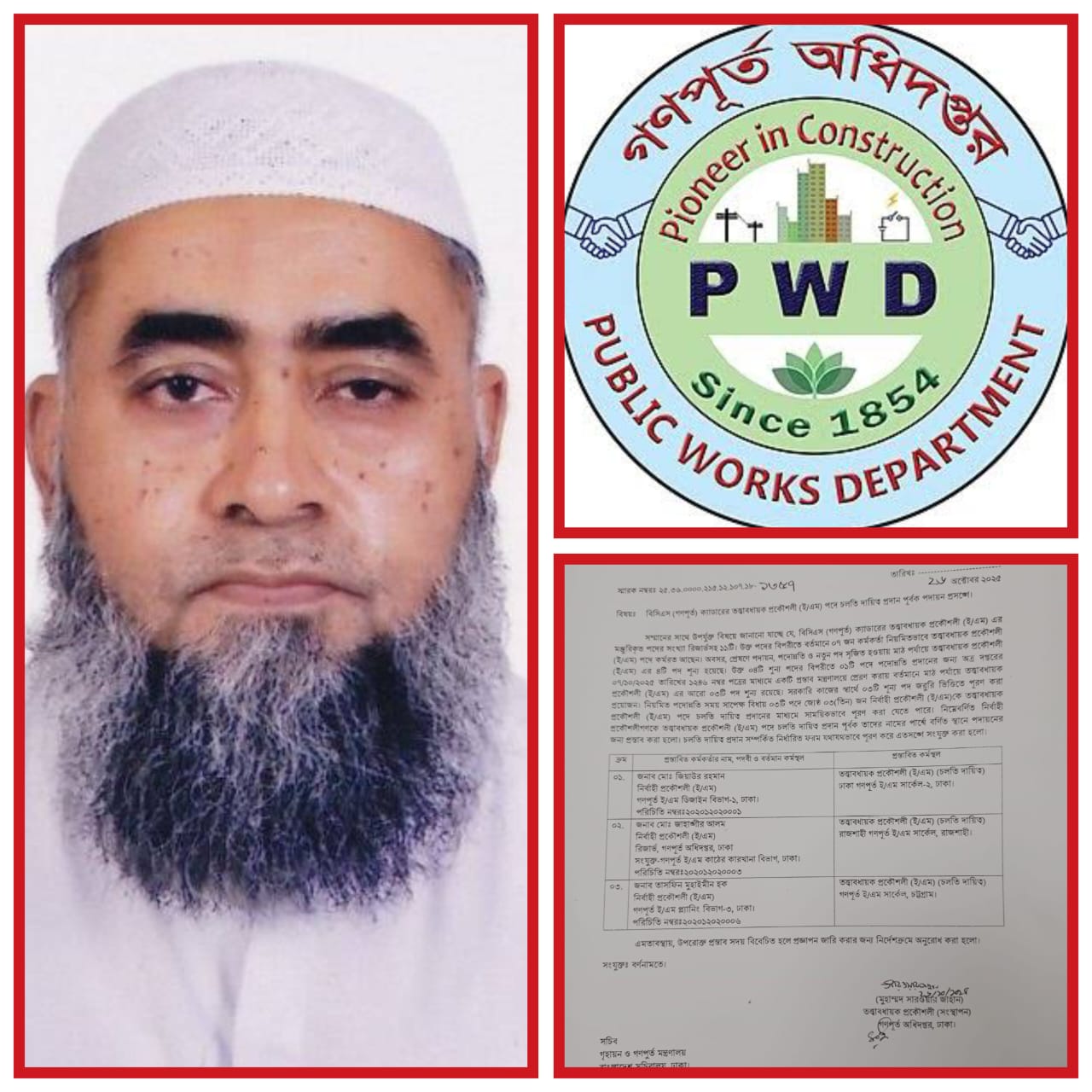পুলিশ ও সামরিক অসদাচরণ বিচারে প্রমাণের মানদণ্ড

- আপডেট সময় : ০৪:৫১:২৭ অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৮৫ বার পড়া হয়েছে
ইংল্যান্ডে পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণের বিচারে প্রমাণের যে মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়, তা বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক; কারণ বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক সূত্রে ব্রিটিশ কমন ল’ বা সাধারণ আইনের উত্তরাধিকার বহন করে। যেহেতু আইনের ছাত্র নন, এমন পাঠকও এই নিবন্ধটি পড়বেন, সেহেতু মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কমন ল’ বা সাধারণ আইন কী, তার একটি সহজ ধারণা এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কমন ল’ বা সাধারণ আইন হলো এমন একটি আইনি ব্যবস্থা, যেখানে আইনগুলো শুধু আইনসভা বা আইন প্রণেতাদের মাধ্যমে প্রণীত নয়, বরং বিচারিক সিদ্ধান্ত বা ‘নজির (precedents)’-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।
বিচারকেরা এই পূর্ববর্তী রায়গুলোকে একই ধরনের নতুন মামলায় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। এর মাধ্যমে এমন বাধ্যতামূলক আইনি নীতি তৈরি হয়, যা আইনি ফলাফলের ধারাবাহিকতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থাটি ইংল্যান্ডে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এ আইনগুলোর ভিত্তি হলো স্টেয়ার ডিসিসিস (স্ট্যান্ড বাই ডিসিশন) বা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নীতি, যা ন্যায়, সংগতি ও স্থিতি সমুন্নত রাখে এবং উচ্চ আদালতের এমন সিদ্ধান্তগুলো নিম্ন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় হয়ে থাকে। আইন শাস্ত্রে এটাই কমন ল’।
এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ইংল্যান্ডে নিয়ন্ত্রিত পেশাদার প্রতিষ্ঠান বা সেবাগুলোর (regulated professional institutions/services) অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা তদন্তে সর্বদা দেওয়ানি মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়; অর্থাৎ সম্ভাবনার ভারসাম্য (balance of probabilities)—অপরাধমূলক মানদণ্ড ‘যুক্তিসংগত সন্দেহাতীত (beyond reasonable doubt)’ নয়। এই মানদণ্ড পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং চিকিৎসা ও আইনসহ সব নিয়ন্ত্রিত পেশায়ও (regulated profession) প্রযোজ্য। মূল নীতিটি হলো—‘ক্ষমতা যত বেশি, জবাবদিহিতার দায় তত বেশি।’
এই মানদণ্ড নৈতিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেই বলেছি, বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক সূত্রে ব্রিটিশ কমন ল’ বা সাধারণ আইনের উত্তরাধিকার বহন করে, যে কারণে এ-জাতীয় আইন বোঝার ও প্রয়োগ করার এক সহজাত প্রশাসনিক ও মানসিক চিন্তার অবকাঠামো এখানে রয়েছে। অতএব বাংলাদেশের আইনে এই নীতি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে দেশের পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা, জনআস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সদাচরণ শক্তিশালী হয়। রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যাদের হাতে ন্যস্ত—যেমন পুলিশ ও সেনাবাহিনী, তারা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। এসব ক্ষমতা হলো—আটক করার ক্ষমতা, বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা এবং চরম ক্ষেত্রে জীবন নেওয়ার ক্ষমতা। সাধারণ যুক্তিবোধ বলে, এ ধরনের ক্ষমতার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে সমানভাবে আসে অসাধারণ দায়বদ্ধতা।
বাংলাদেশ একটি কমন ল’ বিচারব্যবস্থা হিসেবে একই ধরনের আইনি ভিত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। তবে এর পুলিশ ও সামরিক শৃঙ্খলাবিধি এখনো পুরোনো ও অস্পষ্ট, যার ফলে জবাবদিহিতা অনিয়মিত থেকে যাচ্ছে। বিশেষত বাংলাদেশের পুলিশ গোড়াতেই গঠিত হয়েছে। দেশের মানুষের সেবার জন্য নয়, বরং ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজনে, ঔপনিবেশিকতা প্রলম্বিত করার বিশেষ উদ্দেশ্যে, যার মৌলিক দর্শন ছিল ত্রাসন, দমন ও শাসন, অর্থাৎ ভীতিসঞ্চার এবং দমনের মাধ্যমে শাসন জারি রাখা।
২. ইংল্যান্ডের কাঠামো
২.১ পুলিশ কর্মকর্তা : ‘Police (Conduct) Regulations 2020’ স্পষ্টভাবে বলে, অসদাচরণ শুনানিতে দেওয়ানি মানদণ্ড প্রযোজ্য। ‘College of Policing’-এর নির্দেশিকাতেও বলা আছে, অভ্যন্তরীণ তদন্তে সম্ভাবনার ভারসাম্য ব্যবহার করা হয়। R (Green) v Police Complaints Authority [2004] UKHL 6 মামলায় হাউস অব লর্ডস নিশ্চিত করেছে, শৃঙ্খলা শুনানি (discipline hearing) একটি নিয়ন্ত্রক (regulatory) প্রক্রিয়া, অপরাধমূলক নয়। যদি অপরাধমূলক মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়, তাহলে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা কার্যত অসম্ভব হয়ে যাবে।
২.২ সশস্ত্র বাহিনী : ‘Armed Forces Act 2006’ সামরিক আদালতে (courts martial) অপরাধমূলক মানদণ্ড এবং প্রশাসনিক/শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় দেওয়ানি মানদণ্ড আলাদা করেছে। ‘Service Complaints Ombudsman’-এর নির্দেশিকাও নিশ্চিত করে, অভ্যন্তরীণ পেশাগত জবাবদিহিতা সম্ভাবনার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে হয়।
২.৩ চিকিৎসক পেশাজীবী : Re B (Children) (Care Proceedings: Standard of Proof) [2008] UKHL 35 মামলায় হাউস অব লর্ডস নিশ্চিত করেছে, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও যত্ন-সংক্রান্ত মামলায় দেওয়ানি মানদণ্ড প্রযোজ্য। General Medical Council v Adeogba [2016] EWCA Civ 162 মামলায় আপিল আদালত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, চিকিৎসকের fitness-to-practise শুনানি একটি নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, অপরাধমূলক নয় এবং তাই সম্ভাবনার ভারসাম্যের ভিত্তিতেই বিচার হয়।
২.৪ অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত পেশা (Regulated profession) : নার্সিং, আইন পেশা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত পেশায়ও একই মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়। Nursing and Midwifery Council এবং Solicitors Regulation Authority উভয়ই পেশাগত অসদাচরণের বিচারে দেওয়ানি মানদণ্ড প্রয়োগ করে।
৩. দেওয়ানি মানদণ্ডের যৌক্তিকতা
পেশাগত অসদাচরণের বিচারে দেওয়ানি মানদণ্ড প্রয়োগের যৌক্তিকতা হলো—
(১) অধিক দায়িত্বশীলতা : বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকা কর্মকর্তাদের সাধারণ কর্মচারীদের তুলনায় উচ্চ মানদণ্ডে জবাবদিহি করতে হবে।
(২) ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা : অসদাচরণ প্রায়ই এমন প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটে, যা অপরাধমূলক মানদণ্ড পূরণ করে না, তবুও জনআস্থা রক্ষার্থে শাস্তি প্রয়োজন।
(৩) পেশাগত সামঞ্জস্য : চিকিৎসক, আইনজীবী, সৈনিক ও পুলিশ সবার জন্য একই প্রমাণের মানদণ্ড প্রযোজ্য।
(৪) বিচারিক কর্তৃত্ব : Re B (Children) এবং GMC v Adeogba মামলাগুলো ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত করেছে, নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম সর্বদা দেওয়ানি মানদণ্ডে বিচার হয়।
৪. তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ : বাংলাদেশ
৪.১ বর্তমান কাঠামো
বাংলাদেশের পুলিশ শৃঙ্খলাবিধি এখনো ‘Police Regulations of Bengal (1943)’-এর ওপর ভিত্তি করে, আর সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হয় ‘Bangladesh Armed Forces Act 1952’ দ্বারা। উভয় ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ তদন্তে প্রমাণের মানদণ্ড অস্পষ্ট।
৪.২ ব্যবহারিক ফলাফল
এই অস্পষ্টতার কারণে অসদাচরণ—যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, হেফাজতে নির্যাতন, ও ক্ষমতার অপব্যবহার—প্রায়ই প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে শাস্তিহীন থেকে যায়, আর অপরাধমূলক কর্মের বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এর ফলে দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয় এবং জনআস্থা বিনষ্ট হয়।
৪.৩ প্রস্তাবিত সংস্কার
বাংলাদেশের উচিত পুলিশ ও সামরিক শৃঙ্খলা-বিচারে দেওয়ানি মানদণ্ড স্পষ্টভাবে আইন দ্বারা নির্ধারণ করা। এর মধ্যে থাকতে পারে—
(১) আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে বিভাগীয় তদন্ত সম্ভাবনার ভারসাম্যের ভিত্তিতে বিচার হবে।
(২) পুলিশ ও সামরিক অসদাচরণে স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুলিশের জন্য ইনডিপেনডেন্ট পুলিশ কমপ্লেইন্ট কমিশন গঠনের প্রস্তাব করতে পারি, যা হবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি স্থায়ী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ।
(৩) শৃঙ্খলা-বিচারের ফলাফল জনগণের কাছে প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
(৪) অসদাচরণ রিপোর্টকারী কর্মকর্তাদের জন্য হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা বিধান। এই সংস্কারগুলো জনআস্থা ফিরিয়ে আনবে, প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করবে, জনজবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে।
৫. কঠোর ক্ষমতাসম্পন্ন (hard power) প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর দায়িত্ব
পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তারা সাধারণ রাষ্ট্রকর্মচারী নন। তারা রাষ্ট্রের কঠোর ক্ষমতা (hard power) প্রয়োগ করেন, যেমন অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার, আটক ক্ষমতা প্রভৃতি। এগুলো সার্বভৌমত্ব রক্ষা-বিষয়ক প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। তাই তাদের অবশ্যই উচ্চতর মানদণ্ডে জবাবদিহি করতে হবে।
ইংল্যান্ডে দেওয়ানি মানদণ্ড নিশ্চিত করে যে, জবাবদিহিতা অপরাধমূলক প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং জননিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশেও এই নীতিকে আইনে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
ইংল্যান্ডে পেশাগত অসদাচরণের বিচার সর্বদা সম্ভাবনার ভারসাম্যের ভিত্তিতে হয়—তা পুলিশ, সামরিক বাহিনী, চিকিৎসক বা আইনজীবী যে-ই হোক না কেন। এই মানদণ্ড নৈতিক, ব্যবহারিক ও ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগযোগ্য, যা বলপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ওপর অধিকতর দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন।
বাংলাদেশ একই কমন ল’ উত্তরাধিকার বহনকারী দেশ হিসেবে তাদের পুলিশ ও সামরিক শৃঙ্খলাবিধিতে এই মানদণ্ড আইন দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত। জবাবদিহিতা যেন অপরাধমূলক প্রক্রিয়ার কাছে বন্দি না হয়ে বরং একটি ন্যায্য ও দেওয়ানি মানদণ্ডের তদন্ত দ্বারাও নিশ্চিত হতে হবে।
ইউনিফর্ম ও ক্ষমতা সমালোচনা ও জবাবদিহিতার হাত থেকে রক্ষাকবচ নয়। এগুলো দায়িত্বের প্রতীক, আর দায়িত্ব মানেই সম্ভাবনার ভারসাম্যের ভিত্তিতে দায়িত্ব আর বল প্রয়োগের অধিকারের সমানুপাতিক জবাবদিহিতা।
লেখক : আফযাল যামী, কাউন্সেল, সুপ্রিম কোর্ট অব ইংল্যান্ড
মোহাম্মদ শাহ্ আলম, শিক্ষাবিদ, সিটিজেন অ্যাক্টিভিস্ট, ইংল্যান্ড